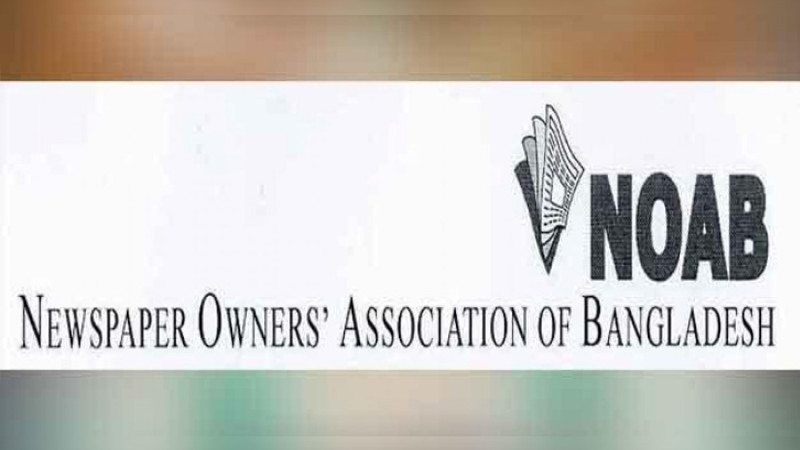ভারত থেকে ৫৩টি নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশের হাওর, খাল ও নদীতে পানি আসে। সে পানি যায় বঙ্গোপসাগরে। গবেষণায় দেখা গেছে, বঙ্গোপসাগরে যাওয়া পানির ৫৬ ভাগ ভারতের, ৪৪ ভাগ বাংলাদেশের। তবে বাংলাদেশ হয়ে এই পানি সাগরে যেতে পথে পথে পড়ে নানা বাধার মুখে। নদীর নাব্য সংকট, অপরিকল্পিত বাঁধ ও পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়ি মহাসড়কই পানির প্রবাহে মূল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখনই ভারত থেকে আসা অতিবৃষ্টির পানি বাংলাদেশের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব এলাকায় আটকে বন্যা সৃষ্টি করে।
নদী বিষয়ক সংগঠন রিভারাইন পিপল বাংলাদেশের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের তিন পাশ দিয়ে ভারতের ৫৩টি নদী দিয়ে পানি ঢোকে। এরমধ্যে বড় নদীগুলো হলো—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা। মাঝারি নদীগুলোর মধ্যে আছে মহানন্দা, ধরলা, তিস্তা, দুধকুমার, ভোগাই, সোমেশ্বরী, যাদুকাটা, গোমতী, মনু, খোয়াই ও ফেনী। ছোট নদী আছে ৩৯টি। এছাড়াও ছোট ঝিরি ও ছরা দিয়েও পানি বাংলাদেশে আসে। কেবল একটি নদী দিয়ে বাংলাদেশ থেকে পানি যায় ভারতে। ওই নদীর নাম কুলিক। সেটি অবশ্য মৃতপ্রায়।
বন্যার পানি প্রবেশের রুট: ভারত থেকে আসা পাহাড়ি ঢল বাংলাদেশের ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় তিন শতাধিক নদ-নদী দিয়ে সাগরে মেশে। এই পথগুলোই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ভারত থেকে আসা বন্যার পানি প্রধান তিনটি রুট দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকে। এ বিষয়ে রিভারাইন পিপল-এর মহাসচিব শেখ রোকন বলেন, ‘এর একটি হলো গঙ্গা। যার পানি রাজশাহী দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকে। দ্বিতীয়টি ব্রহ্মপুত্র। যার পানি কুড়িগ্রাম দিয়ে প্রবেশ করে। অপরটি হলো মেঘনা। হাওর অঞ্চল, সুরমা, কুশিয়ারা, সোমেশ্বরী, জাদুকাটাসহ ১৭টি নদী আছে, যেগুলোর পানি ভারত থেকে এসে হাওর অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে। এগুলো সব মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়।’
দুই ধরনের বন্যা: একসময় বাংলাদেশে পাঁচ ধরনের বন্যায় সমতল ভূমি প্লাবিত হতো বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। তবে এখন দুই ধরনের বন্যা বেশি পরিচিত। শেখ রোকন বলেন, ‘একটি উপকূলীয় বন্যা। এটি দক্ষিণাঞ্চলে হয় ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের সময়। আরেকটি পাহাড়ি ঢল। পাহাড়ি এলাকার বৃষ্টি গড়িয়ে নিম্নভূমিতে চলে আসে। এটি আকস্মিক বন্যা। দূরে কোথাও বা প্রতিবেশী দেশে প্রচুর বৃষ্টি হলে সেই পানি নদীপথে নিচের দিকে আসতে থাকে। এতে বেশি ক্ষতি হয় বাংলাদেশের। সাধারণত এ ধরনের পাহাড়ি ঢল দেখা যায় মে মাসে। যা ইতোমধ্যে তিনবার হয়েছে। আরেকটি আছে মৌসুমি বন্যা। যখন মেঘগুলো হিমালয়ে ধাক্কা খায়, তখন প্রচুর বৃষ্টি হয়। সেই পানি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে যায়। এই বন্যা তিন অববাহিকাতেই হয়। তিন অববাহিকায় যদি আলাদা আলাদা সময়ে হয় তখন বাংলাদেশের তেমন বিপদ হয় না। পানি নেমে যাওয়ার সময় পায়। কিন্তু একই সময় তিন অববাহিকায় বন্যা হলে দেশের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক প্লাবিত হয়। বেশি দিন পানি আটকে থাকে। এবারও তাই হচ্ছে।
শেখ রোকন বলেন, মেঘনায় যখন পানি আসে তখন যমুনার পানি নামতে পারে না। আবার একই সময় যদি গঙ্গা দিয়ে পানি আসে, তখন মেঘনা ও যমুনার পানি নামতে পারে না। এবার মেঘালয়, আসাম, অরুণাচল, সিকিম, ভুটান, নেপালে বৃষ্টি হয়েছে। তাই মেঘনা ও যমুনায় বন্যা দেখা দিয়েছে। এরপর বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি হওয়ায় গঙ্গাতেও বন্যা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ প্লাবিত হয়েছে।
বন্যা-চক্র: শেখ রোকন জানালেন, বন্যা একটি চক্র মেনে চলে। পাঁচ থেকে সাত বছর পর পর বড় বন্যা হয়। ২০১৭, ২০১৪, ২০০৭-০৮, ২০০৪, ১৯৯৮, ১৯৯৪ এবং ১৯৮৮ সালে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। এই সাইকেলটা মেনে এবারও বন্যা হয়েছে।
পানি কেন সাগরে যেতে পারছে না: বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ৮০ ভাগ ভূমিই নদ-নদী অববাহিকায় পড়ে। ছোট বড় মিলিয়ে নদ-নদী আছে তিন শতাধিক। এগুলোর কোথাও না কোথাও সারা বছর ভাঙন লেগেই থাকে। বর্ষায় ভারত থেকে আসা ঢলে এ ভাঙন আরও তীব্র হয়। যে পরিমাণ পানি আসে তা বাংলাদেশের বড় নদীগুলো ধারণ করতে পারে না।
বন্যা বড় হওয়ার বিষয়ে শেখ রোকন বলেন, ভারতের মেঘালয় ও আসামে অনেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে। তারা হাইওয়ে করছে। বন উজাড় করছে। বিভিন্ন খনিতে কাজ চলছে। পাহাড়ে যখন গাছপালা থাকে তখন পলিমাটি ধুয়ে নদীতে আসে না। কিন্তু যখন গাছ না থাকে তখন সব ধুয়ে নদীতে যায়। এতে বাংলাদেশের নদীর গভীরতা কমছে ও পানি সমতলে চলে আসছে। সুরমা নদীর তলদেশে বর্জ্য ও পলিথিনের স্তর পেয়েছি আমরা। এ কারণেও নদী পানি ধরে রাখতে পারছে না। এছাড়া যেসব ছরা দিয়ে হাওরে পানি যেত সেগুলোও দখল হয়েছে, সংকুচিত হয়েছে। পানি প্রতিবন্ধকতার আরও কিছু বড় কারণ আছে, যেমন—নাব্য সংকট, প্লাবন ভূমিতে বাঁধ, সড়ক ও স্থাপনা। এসব জায়গা আগে পানি ধারণ করতো। কিন্তু সেগুলো বন্ধ হয়েছে। জনবসতি হয়েছে। পানি যাওয়ার জায়গা পাচ্ছে না। আমাদের মহাসড়কগুলো পূর্ব-পশ্চিম দিকে আড়াআড়ি করে নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো হওয়া উচিত ছিল উত্তর-দক্ষিণে। পূর্ব-পশ্চিমে মহাসড়ক হওয়ায় পানি সহজে নামতে পারে না।
বালু উত্তোলন: শেখ রোকন বলেন, দেশের সবকটি নদী দিয়ে বালু উত্তোলন করা হয়। নির্বিচারে বালু উত্তোলন করায় নদীর গতিবেগ নষ্ট হয়। ভাটিতে গিয়ে নদীর কোথাও চর পড়ে। এতে পানি প্রবাহও ঠিক থাকে না। এ ছাড়া উজান থেকে প্রবাহ স্বল্পতার কারণেও নদী ভাঙছে। প্রবাহ কমায় উজান থেকে আসা মাটি ও বালু মাঝপথে আটকে যাচ্ছে। তখন তীরে পানির চাপ বাড়ে, বন্যা হয়।
পাহাড়ি ঢল দ্রুত সাগরে নামাতে হলে: হাওর মাস্টারপ্ল্যানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বুক চিরে যাওয়া নদীগুলো দিয়ে ১ লাখ ৫৯ হাজার কিউসেক (এক কিউসেক মানে প্রতি সেকেন্ডে এক ঘনমিটার পানির প্রবাহ) সাগরে যায়। মোট যত পানি সাগরে নামে তার ৫৬ ভাগ ভারত থেকে আসে। ৪৪ ভাগ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বৃষ্টিপাতের। আর তাই পাহাড়ি ঢল দ্রুত সাগরে নামাতে হলে বাংলাদেশের নদীর প্রবাহ ঠিক রাখতে হবে বলে জানান শেখ রোকন। এছাড়া, প্লাবন ভূমিতে উন্নয়ন কাজ না করা, হাওর অঞ্চলের নদীগুলোর নাব্য ফিরিয়ে আনা এবং নির্বিচারে বালু উত্তোলন বন্ধের পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।